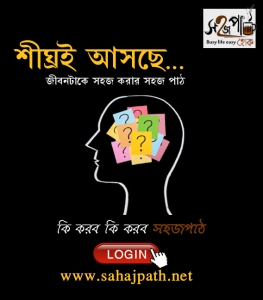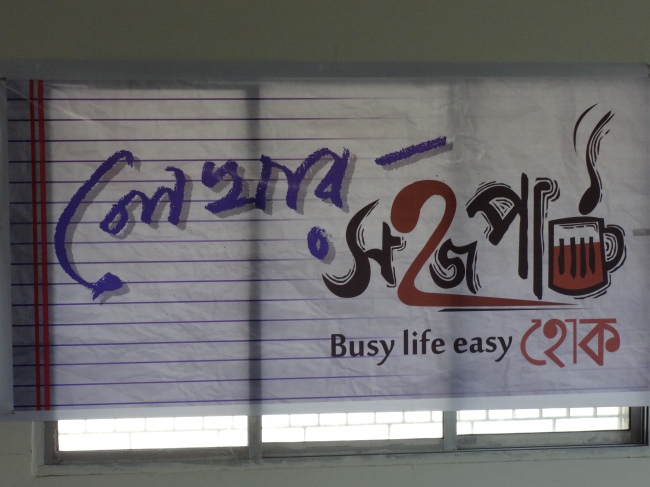জলঙ্গীর জল মাটি
বর্ষা শেষে এখনও হটাৎ হটাৎ করে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি। ‘গৈ-গেরামের পাঁচালি’র লেখক আনসার উদ্দিন আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন হারিয়ে যাওয়া ঘর ছাওনির কথা।
জলঙ্গীর জল মাটি
আনসার উদ্দিন
দু’ হাজার সালের বড় বন্যার পর মাটির বাড়ি গ্রামাঞ্চলে খুব একটা চোখে পড়ে না। হাতে গোনা কয়েকটা বছরে গ্রামের এমন পরিবর্তন ভাবা যায় না। অথচ গ্রাম মানেই মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনি। যারা ঘরে খড়ের ছাইনি দেওয়ার কাজ করত তাদের বলা হত ঘরামি। ‘ঘারমি’ শব্দটা দিন দিন গ্রামীন শব্দ-বন্ধ থেকে মুছে যাচ্ছে বলা যায়। অথচ একটা প্রবাদ কিছুদিন আগেও মানুষের মুখে মুখে ফিরত –‘ঘরের তুমি ঘরের আমি, ঘর ছাইবে ঘরামি’।
হ্যাঁ ঘর ছাওয়াই তো ঘারমির কাজ। আমাদের এ দিকে এক সময় কেলো ঘরামির খুব নাম ডাক ছিল। কেলো ঘরামির হাতে ছাওয়া ঘরে নিশ্চন্তে শুয়ে থাকা যায়। যতই ঝড়-জল হোক, বর্ষা –বাদলা হোক এক ফোঁটা বৃষ্টি ঘরের মেঝেতে পড়বে না। অন্য ঘারমির ছাওয়া ঘরে বর্ষার জল ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকতই। সে কারণে কেলো ঘারমির চাহিদা ছিল খুব বেশি। কিন্তু একা কেলো ঘরামি কত শত ঘর ছাইবে। কেলো ঘরামিকে না পাওয়া গেলে তখন অন্য ঘরামির দ্বারস্থ হতে হয়। তারা চালে ওঠার আগে জিজ্ঞেস করে নিত, হ্যাঁগো গেরস্থ কী ছাউনি নিবা? বাড়িওয়ালা আশ্চর্য হয়ে বলত, কী ছাউনি মানে ? বলছি ঠোকাই, দেশি না একোনা ওকোনা?
সাধারণভাবে ঠোকাই দেশি ছাউনির কথা না জানা থাকলেও একোনা ওকোনা ছাউনির কথা জানা ছিল না। পরে অবশ্য ঘর ছাওয়ার নানান রকফেরের কথা জানতে পেরেছিলাম। এর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাউনির নাম হল ‘ঠোকাই’। ঠুকে ঠুকে ছাওনির কাজ করা হয় বলে এমন নাম করণ। ‘ঠোকাই ছাউনিতে খড়ের পরিমাণ লাগে অনেক বেশি। বাঁশের বাতা দড়িও লাগে সেই অনুপাতে। যে যে লোকের পক্ষে ঘরে ‘ঠোকাই’ ছাউনি দেওয়া সম্ভব হত না। পাড়া গাঁয়ে যে কারণে একটা কথা বেশ চালু ছিল, তা হল- বাঁশ কাবারি পাটের দড়ি/‘ঠোকাই ছাউনির পায়ে পড়ি।
এত এত খড় ও অন্যান্য উপকরণের আধিক্যের হেতু বেশির ভাগ মানুষ দেশি ছাউনি দিত চালে। আমাদের গ্রামের গাঁয়ের কেলো ঘরামি কে বলতাম কেলো চাচা। তাকে একবার শুধিয়েছিলাম,ঠোকাই আর দেশি ছাউনির কথা জানি কিন্তু একোনা ও ওকোণা ছাউনি আবার কীরকম।
কেলো ঘারমি হাসতে হাসতে বলেছিল, জব্বর প্রশ্ন করলেক বটে ভাইপো। যারা কাঁচা ঘরামি তারাই একোণা ওকোণা ছাউনি দেয়। এই ছাউনিতে ঘরে টপ টপিয়ে পানি ঝরে। তখন গেরস্থ বউ ছেলেমেয়েদের হাত ধরে একবার ঘরের একোণে তারপর ওকোণের দিকে ছোটাছুটি করে, বুঝেছ?
কেলো ঘারামির কথায় ঘরের একোণ ওকোণ ছাউনির রহস্যভেদ করতে পারলাম। কিন্তু এখন গ্রামাঞ্চলে খড়ের চালাঘর আগের মতো চোখে পড়ে কই?বড় বড় খড়ের মাঠগুলো এখন চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। শরতের প্রাক্কালে যখন খড়ের মাঠজুড়ে সমস্ত কাশফুল ফুলে উটত খন মনে হত সত্যি সত্যি বান ডেকেছে। এমন দৃশ্য আর তেমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। এখন গ্রামের প্রতিটি বাড়িই পোড়া ইঁটের গাঁথানি দিয়ে তৈরি। প্রায় প্রতিটি গাঁয়ের উপান্তে গজিয়ে উঠছে ইঁটভাটা। তার কালো ধোঁয়া গাঁয়ের নির্মল আকাশ বাতাস কে দুষিত করছে। আমরা প্রতিদিন সকালে সূর্যের আলো ফুটলেয় অয় কালো ধোঁয়া উড়তে দেখি। দেখতে দেখতে সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা নামে। চার পাশে হামা দিয়ে আন্ধকার এগিয়ে আসে। ইঁটভাটার চিমনির ধোঁয়া আন্ধকারে ডুবে যায়। আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হই। আশ্বস্ত হই, কিন্তু স্বস্তি মেলে কই! শ্বাস –প্রশ্বাসে ইঁট ভাটার দুষিত কার্বন আমাদের ফুস্ফুসের রন্ধে রন্ধে ঢুকে পড়েছে। কচি কাঁচা থেকে বুড়ো হাবড়া মানুষের খুক খুকে কাশি থেকে ঘুষ ঘুষে জ্বর। সন্ধে হলেই সেই জ্বর আর কাশি পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে যে। আমাদের গাঁয়ের কান চোয়াল ঘেঁষে বয়ে গেছে জলঙ্গী নদী। নদীর পাড়েই গজ়িয়ে উঠেছে কয়েকটি ইঁটভাটা। তার প্রত্যেকটি চিমনি বেয়ে কালো ধোঁয়ার পতকা নদীর ওপার অবদি উড়ে যায়। উড়তে উড়তে আরও দূর আকাশের সীমানায় হারিয়ে যায়। কিংবা অন্য একটা ইঁট ভাটার চিমনির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যায়।
ইঁট বানানোর প্রধান উপকরণ হচ্ছে মাটি। মাটিকে আমরা র্ধমীয় মোড়কে বলে থাকি মা খাকি। ‘খাক’ কথার অর্থ ছাই, ভস্ম। অন্য অর্থে সেবক বা সেবিকা। বাস্তবিকই তাই। এই মাটিতেই আমাদের জন্ম, মৃত্যু। এই মাটি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই মাটিতে আমরা লালিত পালিত হচ্ছি। আমাদের খিদের অন্ন খুঁজে পেতে হাজার বছর ধরে লাঙল আর ট্রাকটারের সুতীক্ষ ফালের আগায় বার বার ক্ষত বিক্ষত করেছি। কিন্তু এতেও তেমন কিছু সমস্যা হয়নি। সমস্যা তৈরি হয়েছে হাল আমলের অগুনতি ইঁট –ভাটায়। এই সব ভাটায় মাটির যোগান দিতে চাষ যোগ্য জমি থেকে কেটে ফেলা হচ্ছে। সামান্য অর্থের প্রলোভনে চাষি বাসী মানুষ মাটি বিক্রি করে ফেলছে। এতে তামাম মাট জুড়ে তৈরি হয়েছে ক্ষতের আকারে অসংখ্য গর্ত গাবা। মাঠ ময়দানের এমন হতশ্রী দৈন্য দশা আগে কখনো দেখিনি। এখন দেখছি। নদী পাড়ে যে সব ইঁট ভাটারগুলো গজ়িয়ে উঠেছে সেখনকার অবস্থা চাক্ষুষ না করলে বিপর্যয়ের মাত্রা অনুধাবন করা মুশকিল। জলঙ্গীকূলের মানুষ আমি। এই নদীর জল বাতাসে কাল লালিত হয়েছে। সে কারণে জলঙ্গীর প্রতি আলাদা মমত্ববোধ তৈরি হয়েছে। প্রতিদিন দেখছি নদী পাড়ের মাটি যে সি পি নামক যন্ত্র দানবের নির্মম থাবায় উপড়ে ফেলা হচ্ছে। উপড়ে পড়া সেই সব মাটি বিভিন্ন ট্রলিতে করে ইঁটভাটায় কৃত্রিম পাহাড় বানানো হচ্ছে। শুধু এক পাড় নয়, দুপাড়ে এমন ভগ্ন দশা দেখে নদীকে আর নদী বলে মনে হয় না। একটু একটু করে চেনা নদী অচেনা হয়ে যাচ্ছে। পার্টি,পঞ্চায়েত , প্রশাসন আর গাঁয়ের উঠতি মস্তানদের দল একাজে মদত জুগিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে সামান্য বর্ষার বাড়াবাড়িতে নদী হামা টানতে টানতে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে। বর্ষা শেষে খাদানগুলোতে নতুন করে পলি জমে। এই নরম পলি মাটিতে যে শক্ত পোক্ত ইঁট হয়। তার কদর কত! যে কারণে মাটি খাদান গুলো আরো গভীরতর হচ্ছে, নদী পাড় বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেছে না। ইঁট ভাটার চিমনি দিয়ে গল গলিয়ে যে বিসাক্ত ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। ইঁট ভাটার অভিশাপে আমরা রোগ জর্জর জলংঙ্গীপাড়ের মানুষ। এক প্রতিবেশি হাঁপানি কাশির শব্দে অন্য প্রতিবেশির ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমরা অসহায় ভাবে নদী পাড়ের দিকে চেয়ে থাকি। বর্ষার প্র শরং কাল। সেই শরতে আগের মত নদীর পাড়ে কাশ ফুল ফুটতে দেখি না। আমাদের উংসবের দিনগুলো বড় নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। তখন শুধু ইঁটা ভাটার কালো ধোঁয়ার পাশ কাটিয়ে শরতের আকাশ দেখি। দেখি টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ওড়াওড়ি। তবুও ঐ মেঘগুলো দেখেও আমাদের বিভ্রম কাটে না। শুধু মনে হয়, অগুলো বুঝি শরতের মেঘ নয়, টুকরো টুকরো কাফন। যে কাফন গুলো কালো ধোঁয়ার আড়ালে নদী পাড়ের দু’ পাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে।
বিদ্যাদান
সহজ পাঠ’এ নতুন লেখা ‘বিদ্যাদান’ । লিখছেন দোলন গঙ্গোপাধ্যায়।
নতুন এলে পুরোনোকে যেতেই হবে, এ কোন নতুন কথা নয়।ফলে আমাদের প্রায় গোটা ছোটবেলা কালের গর্ভে বিলীন হল।গড়িয়াহাটে বুলেভার্টের বাজার বিদায় নিল, ঘটি গরম চানাচুর বিদায় নিল, গরমের দুপুরে শুন-শান পাড়ায় পাড়ায় হেঁকে-বেড়ানো কুলপী্মালাই হারিয়ে গেল, আর হারিয়ে গেল গৃহশিক্ষক।বাড়িতে এসে পড়ানোর মাস্টারমশাই সম্প্রদায়ও যেন হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলেন।
আমাদের কৈশোরে এত কোচিং ক্লাসের চল ছিল না।উঁচু ক্লাসে, মানে উচ্চমাধ্যমিক কিম্বা অনার্স পরীক্ষার আগে একটি-দুটি বিশেষ ব্যাথার সাবজেক্টে কোচিং-এ যেত ছাত্র-ছাত্রীরা। তার আগে পর্যন্ত প্রায় সব পড়ুয়ারই বাড়ি ব’য়ে এসে বিদ্যা বিতরণের জন্য একজন ক’রে গৃহশিক্ষক মজুত থাকতেন।আমাদের সেই সাবেকী বাড়িতে আমরা চার-পাঁচজন ভাই বোন এবং প্রায় সমবয়সী কয়েকজন কাকা-পিসি একসঙ্গে বড় হচ্ছিলাম।মাস্টারমশাইয়ের ব্যাবস্থা-টা ছিল এরকম, আমার দাদাভাইকে যিনি মাধ্যমিকের বৈতরণী পার করালেন, তার কাছেই আমরা পালা ক’রে নাড়া বাঁধতাম।ফলে একজন মাস্টারমশাই প্রবেশ করলে তিনি বেশ থিতু হয়েই বসতেন।অনেকসময় কাকা পিসিদের আমল থেকেই কেউ কেউ বহাল হতেন।
আমাদের বাড়ির পিছনেই থাকতেন বটু মাস্টার।পাড়াসুদ্ধু সকলে তাকে ঐ নামে ডাকতেন।তিনি সম্ভবত সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।পরণে শ্বেতশুভ্র মিলের ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি, অকাল-বৃদ্ধ, ছোটখাটো মানুষটি আমাদের ইংরিজি পড়াতেন।নেসফিল্ড আর রেন এন্ড মার্টিন থেকে ব্যাকরণ শেখাতেন। তবে যাদের শুধু পাসমার্ক তুললেই চলত, তাদের জন্য তাঁর ঝুলিতে পি.কে.দে.সরকারও ছিল।আমরা হচ্ছি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ যারা ক্লাস ওয়ান থেকেই ইংরিজি পড়তাম।বাংলা মাধ্যম সরকারী স্কুলে পড়তাম, তাই ইংরিজির জন্য ভাল মাস্টার মশাইয়ের খুবই দর ছিল আমাদের বাড়িতে।যদিও আমাদের স্কুলেও যথেষ্ট যত্নসহকারে ইংরিজি শেখানো হত।
সে যাহোক, আমাদের বাংলা মিডিয়াম পাড়ায় বটু মাস্টামশাইয়ের বিশেষ কদর ছিল।তিনি ঘড়ি ধ’রে সন্ধ্যে ছ’টায় ঢুকতেন।অবশ্য তাঁর হাতঘড়ি ছিল না।বাড়ির একটা টাইমপিস-ই তাঁদের পুরো পরিবারের ভরসা ছিল।তাঁর তিন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়ে এবং তিনি ঐ একটি ঘড়ি এ্যালার্ম দিয়ে নিজেদের সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখতেন।তাঁর স্ত্রীও ঐ ঘড়ির এ্যালার্ম-এই ভোর চারটেয় উঠে উনুনে আঁচ দিতেন।তারপর একে একে তাঁর তিন ছেলেমেয়ে কেউ পাঁচটায় কেউ ছ’টায় এ্যালার্ম বাজিয়ে উঠত।আমাদের দোতলার পড়ার ঘরের জানলার রুজু রুজু ছিল মাস্টারমশাইয়ের টিনের চাল।ওদের বাড়ির তীক্ষ্ণ এ্যালার্ম আমাদের সকালের ঘুমে প্রায়শই ব্যাঘাত হানত।মাঝে মাঝে সে ঘড়ি সারাতে দিতে হত। মাস্টারমশাই তখন আমাদের বাড়ি থেকে একটা টাইমপিস ধার ক’রে নিয়ে যেতেন।ঘড়ি ছাড়া তাদের এক দিনও চলত না।
পেশাদার মাস্টারমশাই ছাড়াও সে আমলে আরেক ধরণের গৃহশিক্ষকের চল ছিল।পাড়ার কাকু, পিসি কিম্বা জেঠু গোছের মানুষজনের কাছেও প্রায়ই পড়তে যেতে হত।আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীমহলে যার কোন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তির খবর রটত, তার কাছেই রবিবার সকালে ঠেলে পাঠানো হত আমাদের। এজন্যই প্রায় রবিবার সকালটায় আমার পেট ব্যাথা করত।কিন্তু কি এক কৌশলে দুপুরে মাংস ভাত খাওয়ার আগেই সে পেট ব্যাথা পুরো উধাও।তাছাড়া বাড়ির পন্ডিতরা তো ছিলেনই।আমাদের থেকে সামান্য বড় দাদা কিম্বা কাকা পিসির দলও লেখাপড়ার ব্যাপারে মাতব্বরির সুযোগ পেলে ছাড়তেন না। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!
আমার এগারো ক্লাসে সম্ভবত বটু মাস্টারমশাই প্রয়াত হলেন।আমাকে ইংরিজি আর অঙ্ক পড়াতে আসতেন শান্তিবাবু।তিনি একটি সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।শান্তিবাবুকে মনে পড়ে একটি বিশেষ কারণে।তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত অনুবাদ করতে দিতেন।উনি আসতেন সন্ধ্যের মুখে।সে সময় আমাদের বাড়িতে দুটো বিশালাকৃতি পাতা উনুনে আঁচ ধরানো হত।একটা তোলা উনুনও জ্বালানো হত।ঠাকুমা রান্নাঘরের জানলা দিয়ে কখনো রান্নার ঠাকুর কখনো বা তার বৌমাদের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়তেন, “কই গো সব, এবার উনুন ধরাও, বিকেলের জলখাবার আর কখন হবে!” শান্তিবাবু তক্ষুনি বলতেন, “ঠাকুমার কথাটা ট্রানস্লেশন কর তো!” তারপর যেই উনুনে আঁচ পড়ত আর আমাদের পেল্লাই বাড়িটা ধোঁয়ায় ভরে উঠত, শান্তিবাবু আরও দুলাইন জুড়ে দিতেন, “বাড়িটা ধোঁয়ায় ভরে গেল।ধোঁয়ার জ্বালায় আর বাঁচি না বাবা! কি চোখ জ্বালা করছে!”
সেসময় রেডিওতে পৌনে ছটা থেকে সোয়া ছটা পর্যন্ত “মনের মত গান, মনে রাখার কথা” নামে একটা অনুষ্ঠান হত।শ্রাবন্তী সঞ্চালনা করতেন।আমার বেশ আসক্তি ছিল ঐ ‘মনের মত গান, মনে রাখার কথা’-য়।একদিন ছাদের ঘরে শান্তিবাবু পড়াচ্ছেন।পাশের বাড়ির রেডিও থেকে ভেসে আসছে শ্রাবন্তীর সঞ্চালনা আর ‘মনের মতন গান’।আমারও কানের ভিতর দিয়ে মরমে সে গান পশছে।এবং প্রাণও যথা নিয়মে আকুল হচ্ছে।শান্তিবাবু নিশ্চই সেটা সম্যক অনুধাবন করেছিলেন।তাই আচমকা অনুবাদ করতে দিলেন, “হতাম যদি তোতা পাখি, তোমায় গান শোনাতাম/হতাম যদি বনমায়ূরী, তোমায় নাচ দেখাতাম”।শ্রাবন্তী তখন ঐ গানটিই বাজাচ্ছিলেন।
আমার ছোটবেলায় আরেকজন মাস্টারমশাই ছিলেন।তিনি আমাকে প্রথম শেক্সপীয়রের সঙ্গে পরিচয় করান।তখন বোধহয় ক্লাস ফোরে পড়ি।ঐ মাস্টারমশাই ঠিক আমাকে পড়াতেন না।মানে আমাকে পড়ানোর জন্য তিনি নিযুক্ত হননি।কাকা পিসিদের কাউকে পড়াতেন।আমি পাশে বসে এটা ওটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য জ্বালাতন করতাম ওকে।এখন বুঝি সেটা কেমন বিরক্তিকর ব্যাপার।কিন্তু উনি কোনদিনও বিরক্ত হননি।বড়দের পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে আমার সব উৎপাত হাসিমুখে সহ্য করতেন।একবার সম্ভবত ফার্স্ট টার্মের পরীক্ষায় আমি অঙ্কে একটু ভদ্রলোকের মত নমবর পেয়েছিলাম।ওকে লাফাতে লাফাতে অঙ্ক খাতা দেখাতে গেলাম।উনি খুব খুশী।পরদিনই আমাকে বাংলায় অনূদিত ছোটদের “ট্র্যাজেডী অফ শেক্সপীয়র” উপহার দিলেন।বইয়ের মলাট খুলেই মাস্টারমশাইয়ের মুক্তোর মতন হস্তাক্ষরে লেখা,”অঙ্কে আশাতীত ফলের জন্য আশীর্বাদসহ মাস্টারমশাই”।অঙ্কে ‘আশাতীত’ ফল অবশ্য আমার সারাজীবনে ঐ একবারই হয়েছিল।কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের ঐ উপহার আমার জীবনের এক দিগন্ত খুলে দিল।রোমিও জুলিয়েট, ওথেলো দেসদিমোনা, লিয়র, হ্যামলেট-এ বুঁদ হয়ে গেলাম।
মাস্টারমশাই তখন বেকার ছিলেন।খুবই অভাবী সংসারের ছেলে তিনি।তার টিউশ্যনিতেই ওদের পুরো পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলত।আর তখনকার দিনে ছাত্রছাত্রী ঠ্যাঙ্গানোর পারিশ্রমিকও যৎসামান্যই হত।তবু তিনি আমাকে বই কিনে দিলেন।নিশ্চই তাকে ধার করতে হয়েছিল।সে ধার শোধ করতেও তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।কিন্তু তিনি তার পরোয়াও করেননি।আশ্চর্য!
আমাদের বাড়িতে গানের দিদিমণি ইলা বৌদির বিশেষ আদর ছিল।উনি মাসে কুড়ি টাকার বিনিময়ে সপ্তাহে দুদিন আমাদের গান শেখাতেন।গান শেখানো ছাড়াও তার নিত্যকর্ম ছিল দাদুকে শ্যামাসংগীত শোনানো।তদ্গতভাবে তার “মায়ের পায়ে জবা হ’য়ে” আজও কানে ভাসে।ইলা বৌদির দুই ছেলে। আপ্পা আর ছোটন।তিনি গানের ফাঁকে ফাঁকে তার ঘরকন্নার গল্প করতেন।আপ্পা, ছোটনের গল্প। আপ্পার বাবার গল্প।ঐ ক্যাবলা বয়সে আমি অবশ্য অনেকদিন অবধি বুঝতাম না, এই ‘আপ্পার বাবা’-টি কে।যখন জানলাম নিজের স্বামীকে উনি ‘আপ্পার বাবা’ ডাকেন, তখন বেশ অবাক হয়েছিলাম।
প্রসঙ্গত মনে পড়ে, আমাদের দোতলায় সপরিবারে বিমলবাবু থাকতেন।ওদের পরিবারেও বড় অদ্ভুতরকম স্বামী-সম্ভাষণ চলত। সে বাড়ির মহিলারা তাদের স্বামীকে “আমাদের ভদ্রলোক” ব’লে সম্বোধন করতেন।আমাদের বাড়িতেও মা-কাকিমারা “ওগো, শুনছ” ইত্যদি দিয়ে কাজ চালাতেন। ঠাকুমা দাদুর বিষয়ে ‘উনি’-বাচক শব্দ ব্যবহার করতেন। স্বামীকে কেন নাম ধ’রে ডাকা যায় না, কেন এমন অদ্ভুত ডাকে কেন ডাকতে হয়, সে বয়সে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সেসব বোধগম্য হত না।বড়দের জিজ্ঞেস করলে বলতেন, স্বামী গুরুজন।গুরুজনদের নাম ধরতে নেই।সবে-পাকতে-শুরু বয়সে, যখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গোপন ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে আবছা আবছাভাবে অবহিত হলাম তখন আবার হোঁচট খাওয়ার পালা।স্বামী যদি গুরুজনই হবে, তাহলে গুরুজনদের সঙ্গে ওসব লজ্জার কাজ কি ক’রে সম্ভব?ছিঃ!বড়রা তো বাপু ভারী অসভ্য!
ফেরা যাক গৃহশিক্ষকের গল্পে।আমাদের বাড়িতে শিক্ষকদের একটু বিশেষ সমাদর ছিল।আমার দাদামশায় এবং আমার ঠাকুরদার বাবা দুজনেই ছিলেন শিক্ষক।সে আমলের শিক্ষকদের দারিদ্র সম্পর্কে আমার ঠাকুরদার বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল।তার কৈশোর যৌবন খুবই অর্থকষ্টে কেটেছিল।তাই পরবর্তী জীবনে স্বচ্ছলতা আসার পর তিনি সুযোগ পেলেই মাস্টারমশাইদের সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করতেন। বাড়িতে আমরা তখন প্রায় দশ-বারো জন বিভিন্ন ক্লাসের পড়ুয়া গুলতানি করি।সকাল সন্ধ্যে কলেজ থেকে নার্সারি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীর পড়ার ধ্বনিতে আমাদের বাড়ির আকাশ-বাতাস মুখরিত থাকত।সোম থেকে শুক্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মাস্টারমশাই এবং দিদিমণির আনাগোণা চলত বাড়িতে।তাদের জন্য খেপে খেপে চা জলখাবার তৈরী একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।অনেকে সকালে আমাদের বাড়ির টিউশনি সেরে সরাসরি কর্মস্থলে চলে যেতেন।তারা পড়ানো সেরে আমাদের বাড়ি থেকেই দুটি ডাল-ভাত খেয়ে কাজে ছুটতেন।কেউ আবার কাজের থেকে সরাসরি পড়াতে আসতেন।তাদের জন্যও তৈরী হত রকমারি জলখাবার।একই জলখাবার একই মাস্টারমশাইকে পরপর দুদিন দেওয়া চলত না। তাতে তাদের সম্মানহানির আশঙ্কা। তাদের সকলের রুচি-পছন্দও এক ছিল না।কেউ পছন্দ করতেন লুচি আলুরদম, কেউ আবার ফলারে আগ্রহী ছিলেন।ফলে সকাল বিকেল বিভিন্ন ধারার খাবার প্রস্তূত করতে করতে মা-কাকিমাদের নাজেহাল অবস্থা।দাদুর এই অতিরিক্ত শিক্ষক-আদর যে তারা সবসময় খুব সুনজরে দেখতেন তা নয়, কিন্তু তারা নিরুপায়!
আমাদের বাড়িতে মাস্টারমশাই আদরের আরেকটা ব্যাবস্থা চালু ছিল। মাস্টারমশাই অথবা দিদিমণিরা শুধু নিজের নিজের কাজ সেরেই চলে যাবেন, সেটা নিতান্ত অভদ্রতা।তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের কুশল সংবাদ নেওয়া বাড়ির বড়দের অবশ্য-কর্তব্য ছিল।দিদিমণি হ’লে মা জেঠিমা আর মাস্টারমশাই হ’লে বাবা কাকারা কেউ হাসিমুখে অন্তত একবার আমাদের পড়ার ঘরে ঘুরে যেতেন।জলখাবারও তারাই দিয়ে যেতেন।ওদের এই কুশল বিনিময়ের সময় যত দীর্ঘায়িত হত, ততই আমাদের ফূর্তি! মাঝে মাঝে দাদুও কাজ থেকে ফেরার সময় দোতলায় ঢুঁ মারতেন।দোতলায়ই মূলত আমাদের পড়ার ঘরগুলো ছিল।দুজন- তিনজন কাছাকাছি ক্লাসের ভাইবোনেরা একসঙ্গে পড়তাম।মাঝে মাঝে আবার আমাদের বন্ধুবান্ধবরাও জুটত।গ্রুপ স্টাডিস আর কি!
মাস্টারমশাইদের ছেলেমেয়ে কিম্বা ছোট ভাইবোনেদের কৃতিত্বের খবর এলেও আমাদের বাড়ি থেকে তাদের জন্য উপহার পাঠানো হত।গরমে তাদের পরিবারের জন্য আম, লিচু পাঠানো হত।শীতে নলেন গুড়, পাটালি, মোয়া।দিদিমণিদের কাউকে কাউকে পূজোয় শাড়ি দেওয়া হত। মাস্টারমশাইদের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা মা কাকিমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসতেন।বিভিন্ন পার্বণে তাদের সপরিবার নেমন্তন্ন থাকত।তারা আমাদের যথার্থই আপনজন ছিলেন।
আরেকজন মাস্টারমশাইয়ের কথা না বললে এ আখ্যান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।তিনি লেখাপড়ার নয়, নাচের শিক্ষক।তিনি আমার ছোট পিসিকে মণিপুরী নাচ শেখাতে আসতেন।তার একটি পোষাকি নাম ছিল।কিন্তু সে নামে তিনি আমাদের মহল্লায় পরিচিত ছিলেন না।তিনি প্রথমদিন নাচের আর্ট এ্যান্ড টেকনিক বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন।তারপর থেকে তার নাম হয়ে যায়, আর্ট এ্যান্ড টেকনিক।বলা বাহুল্য, এ নাম তার আড়ালে উচ্চারিত হত।যাহোক, তিনি আমার পিসিকে নাচ শেখানোর জন্য মূলত বহাল হলেও আমরা কুচোকাচারাও তার শিক্ষার প্রসাদ পেতাম প্রায়শই।তাছাড়াও, আমাদের বাড়ির ছাদে ম্যারাপ বেঁধে প্রত্যেকবছর ২৫শে বৈশাখ পালন হত।পাড়ার ছেলেমেয়েরা মিলে কোন বছর শ্যামা, কোন বছর চিত্রাঙ্গদা মঞ্চস্থ করত।পাড়ার বাইরেও কারো আত্মীয় বন্ধু ভালো নাচ, গা্ন, আবৃত্তি করতে পারলে তাকেও পাকড়াও ক’রে আনা হত।স্টেজ রিহার্সালের বেশ কিছুদিন আগে থেকে তারা আমাদের বাড়িতেই বেশীরভাগ সময় কাটা্তেন।এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে টালিগঞ্জ থেকে আমার মাসিরা, মামাতো দাদারা বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য আমাদের বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসতেন।বাড়ি একেবারে গমগম করত।এই অনুষ্ঠানেরও নৃ্ত্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন আর্ট এ্যান্ড টেকনিক।তাকে সহযোগিতা করতেন আমাদের সেজমণি মানে সেজকাকিমা।
আর্ট এ্যান্ড টেকনিকের বিদায়পর্বটা সে বয়সেই আমার মর্মান্তিক লেগেছিল।মর্মান্তিক ওর জন্য তত নয়, যত আমার জন্য।উনি মূলত আমার ছোট পিসিকে নাচ শেখাতেন।আমার ছোট পিসির বয়স তখন কুড়ির কোঠায়।আর্ট এ্যান্ড টেকনিক বলতেন, আমার পিসির সম্ভাবনা আছে।ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পিসি নাচতেনও।ছোটপিসির নাচ শেখার পেছনে একটুখানি ইতিহাস আছে।আমার মায়ের ইচ্ছেতে আমার পিসির নৃত্যশিক্ষা।মা মেয়েদের নাচ শেখা খুব পছন্দ করতেন।তার ইচ্ছা ছিল, পিসির সঙ্গে সঙ্গে আমিও শাস্ত্রীয় নাচ শিখি এবং ভবিষ্যতেও যেন নাচ চালিয়ে যাই।আমার আরেক পিসির বন্ধু ছিলেন শতাব্দী পিসি।শতাব্দী পিসি বেশ ভালো নাচতেন।বিভিন্ন নাচের অনুষ্টানে তিনি মায়ের শাড়ি ধার নিতেন।মায়ের মামারবাড়ি ছিল বেনারসে।মা মামাবাড়ি গেলেই শাড়ি কিনতেন। ফলে তার সংগ্রহে অনেক বেনারসী শাড়ি জমেছিল।সেগুলো পাড়াশুদ্ধ সবাই বিয়েবাড়িতে অথবা কোন জমকালো অনুষ্টানে পরতেন।শতাব্দী পিসি প্রায়ই তার প্রিয় মেজবৌদির শাড়ি প’রে স্টেজে উঠতেন।মা তাতে ধন্য হ’য়ে যেতেন।এহেন শতাব্দী পিসির বিদেশে বিয়ের ঠিক হল।মায়ের বেগুনী-রঙা স্কার্ট পার বেনারসী পরেই শতাব্দী পিসি রেজিস্ট্রি বিয়ে করলেন।সে আমলে রেজিস্ট্রি বিয়ে করতে হত শুধু বিদেশ যাওয়ার জন্যই।মা জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যাঁ রে শতাব্দী, বিয়ের পর নাচ চালিয়ে যাবি তো?” শতাব্দী পিসি বললেন, “সে দেশের বাড়িতে কাঠের মেঝে, নাচ প্র্যাকটিস করব কিভাবে, বৌদি?আর ভারতনাট্যম বুঝবেই বা কে!” মায়ের বুকে শেল বিঁধল!মুখমন্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করল।
একদিন শহরের এক বড় জলসায় আমার ছোটপিসি নাচের আমন্ত্রণ পেলেন।মাস্টারমশাই-ই সেই নিমন্ত্রণ জুটিয়ে এনেছিলেন।বেশ বিখ্যাত আসর।ছোটপিসির এত নামী অনুষ্টানের আমন্ত্রণে মা খুব খুশী হলেন।সবাইকে জানানো হল, পিসি অমুক আসরে সুযোগ পেয়েছেন।কথা পৌঁছল দাদুর কানেও।সঙ্গে সঙ্গে আমার অমন আমু্দে দাদুর অন্য মূর্তি। ভ্রু কুঞ্চিত, মুখ গম্ভীর। মা-কে জরুরী তলব।ভদ্রঘরের মেয়ে পাঁচজনের সামনে নাচবে! ও কি বাইজী নাকি!কি আক্কেল বাড়ির মেজ বৌয়ের!পিসির আসরে নাচা হল না।মা গুম মেরে রইলেন কিছুদিন।তারপর একদিন আর্ট এ্যান্ড টেকনিক-কে বিদায় ক’রে দিলেন।বললেন, “নাচ পাঁচজনকে দেখানোর আর্ট, সিন্দুকে তুলে রাখার নয়!”আমি তখন সবে বাণীচক্রে যেতে শুরু ক’রেছিলাম। আমাকেও নাচ ছাড়িয়ে দিলেন। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,”কি হবে শিখে!” আমার জীবন থেকে নাচের মাস্টারমশাইয়ের পাট চুকল।
আমাদের সেই রূপকথার কৈশোর জুড়ে আরও অনেক গৃহশিক্ষক এসেছেন, গেছেন।তারা কেউ ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু কালে নিকটাত্মীয় হ’য়ে উঠেছিলেন।কেউবা খুব পরিচিত, পারিবারিক বন্ধু ছিলেন।সকলের সঙ্গে অভিজ্ঞতাও একরকম নয়।অনেক অপরিচিত শিক্ষকের কাছে কন্যাস্নেহ পেয়েছি।অনেক অতিপরিচিত পাড়ার কাকু পড়াতে এসে অকারণ গায়ে,পিঠে হাত বুলিয়েছেন।কিন্তু তারা মনে দাগ কাটেননি।গৃহশিক্ষকদের সুখস্মৃতিই আমার সম্বল। সামান্য দক্ষিণায় কত যত্নে, কঠোর পরিশ্রমে তারা আমাদের পরীক্ষা-সিন্ধু পার করাতেন!অত লোকের বাড়িতে মা সদা-ব্যাস্ত থাকতেন,নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কোয়ালিটি টাইমের কোন ধারণা অথবা সুযোগ তার ছিল না। আমাদের সে ঘাটতি মেটাতেন এই মাস্টারমশাই-দিদিমণিরা।কত দুঃখ অভিমানে তারা আমাদের সহায় ছিলেন, কত বিপদে-আপদে তারা রক্ষাকর্তা ছিলেন!
দিন গড়িয়েছে।আমরা এখন জীবন-সায়াহ্নে। চারপাশে আর সে জামানার গৃহশিক্ষকের দেখা মেলে না।এযুগে সবই প্রাতিষ্ঠানিক।লাখ-লাখ টাকা কোচিং ক্লাসের মাইনে।প্রাসাদোপম বাড়ি সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। উন্নয়নের বাজারে তারা ছেলেমেয়েদের ভালো ‘প্রতিযোগী’ গড়ে তোলেন, ‘সহযোগী’ নয়।তারা ‘গ্রুমিং’ করেন, বিদ্যাদান নয়।হয়তো সেই ভাল।যুগোপযোগী হওয়াই তো কাম্য।তবু কোথায় যেন করুণ রাগিণী বাজে।মনে হয়, একালে বাচ্চারা বড় দুর্ভাগা!বটু মাস্টারকে তারা জানলই না!
সেলাই করা, সেলাইহারা
এই লেখাগুলোর নাম মায়াময়। । মায়া লেগে থাকে । গত আশির দশকের জীবন-যাপনে আমরা অনেক কিছু সঙ্গে নিয়ে চলতাম । ইয়ুজ করেই থ্রো করে দিতাম না । সেই লেগে থাকা জীবনের ছায়াছবি এই লেখাগুলোয়। এখন যে জীবন খোলাবাজার ও গোলকায়নের দাপটে রপ্ত করতে হচ্ছে তারই বিপরীতে এই অনতি অতীতের স্মৃতি । ফেলে আসা দিনের ছোট ছোট স্মৃতি সেলাই করে আমাদের উপহার দিলেন বিশ্বজিৎ রায়
বাড়িওয়ালার থাকে সেলাইমেশিন আর ভাড়াটের থাকে গুষ্টির সেলাই , সেলাই করার প্রয়োজন । অন্তত বর্ষা শেষে দুপুর বেলাগুলোতে যখন শরৎকাল আসি আসি করছে অনেক সময়েই একথা মনে হত তার । ইস্কুল থেকে ফিরেছে । অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেশ তুলে রেখেছে ভাঁড়ার ঘরের জানলায় । মা রান্না-বান্না সেরে এসে বলল, ‘তাড়াতাড়ি চানে যা । চান খাওয়ার পাট চুকিয়ে আজ ওপরে যেতে হবে । পুজো আসছে । সেলাই করতে হবে।’ তার মায়ের সেলাই মেশিন ছিল না, কেনার পয়সা ছিল না, ছিল সেলাই করার ইচ্ছে আর গুষ্টির সেলাই । ছিল নীল রঙের একটা সেলাইয়ের কৌটো । তাতে কারোর প্রাণভোমরা থাকত না, থাকত অনেকরকম ছুচ, নানা রঙের সুতোর রিল ও বোতাম । সুচেরা ছোটো থেকে বড়ো । সরু ছোটো ছুচ ছিল ব্লাউজ টেঁকে নেওয়ার জন্য, তার থেকে একটু বড়োটা বোতাম সেলাইয়ের কাজে লাগত ।
জামা প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে গেলেই এক লহমায় সেলাই করে দিত মা । প্যান্টের বোতাম কখন যে কোথায় পড়ে যেত, খুলে যেত খেলতে খেলতে টেরই পাওয়া যেত না । প্যান্টের বোতাম খুলে গেলে বন্ধুরা বলত ‘ এ মা ! তোর পোস্টাপিসে বোতাম নেই।’ কেন যে প্যান্টের বোতাম লাগানোর জায়গাটাকে পোস্ট অফিস মানে পোস্টাপিস বলত সে জানে না । তবে এটা বললে খুব লজ্জা হত । একছুটে সোজা বাড়ি । মা হয়তো তখন অন্য কোনও কাজ করছে । এসে মাকে তাড়া দিত । সেলাই করে দাও , সেলাই করে দাও । আর মাও সব কাজ ফেলে সেলাই করে দিত প্যান্টের বোতাম । প্যান্টটা মাকে খুলে দিত সে । মায়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াত । মা সেলাই কৌটো থেকে সরু ছুচ বের করে সেলাই করতে বসত । সেই যে সেই কৌটোতে থাকত অনেকরকম সুতো ও বোতাম । নীল, কালো, সাদা । প্যান্টের জন্য কালো আর নীল সুতো-বোতামই বেশি লাগত । অনেক সময় আবার সুতোর সঙ্গে বোতামের রং মিলত না । তাতে কী ? পোস্টাপিসে বোতাম লাগানো হয়ে গেলেই মা প্যান্টটা তার দিকে ছুঁড়ে দিত । উঠে যেত ফেলে আসা কাজ শেষ করার জন্য । সে তখনই প্যান্ট পরে এক ছুট্টে খেলার মাঠে । জামার বোতাম খুলে গেলে অবশ্য খালি গা হওয়ার দরকার হত না । জামার বুকের কাছের বোতামটাই হারিয়ে যেত সবচেয়ে বেশি । কোথায় যে পড়ে যেত কখন ! মা জামা পরা অবস্থাতেই বুকের বোতাম সেলাই করে দিতে পারত । সেলাই হয়ে গেলে, বোতামের পেছনে গিঁট দেওয়া হয়ে গেলে মা মাথা নামিয়ে জামা পরা অবস্থাতেই দাঁত দিয়ে ছুচের সুতো কেটে দিত । বুকের বোতাম যেত ভিজে । আর জামায় একটু হলেও লেগে যেত রান্নাঘরের মা মা গন্ধ ।
এইসব ছোটো খাটো সেলাই ছাড়াও মাঝামাঝি সেলাই ছিল কিছু । যেমন রঞ্জিত স্টোর্স থেকে কেনা রুবিয়া ভয়েলের ব্লাউজগুলো ছড়ানো থাকত খাটের ওপর । মা ওপরের, জেঠিমাকে বলত , ‘জানো দিদি আজকালকার ব্লাউজের সেলাইগুলো একদম যায় না।’ মা সন্ধেবেলা তাকে পড়ানোর পর রঞ্জিত স্টোর্সের ব্লাউজ নিয়ে বসত । বাবা তখন রেডিওতে খবর শুনত । ইভা নাগ খবর পড়তেন । একশো ওয়াটের বাল্ব মাঝে মধ্যে লো ভোল্টেজের জন্য কাঁপত । সে মায়ের সেলাই করা দেখত । মা আর একবার করে ব্লাউজের সেলাইগুলোকে টেঁকে নিত । হয়ে গেলে দাঁতে করে ছুচ সুতোকে আলাদা করত ব্লাউজ থেকে । করতে করতে একসময় ছুচের সুতো ফুরোত । তখন আবার রিল থেকে সুতো পরাতে হত ছুচে । তখন মায়ের সঙ্গে একটা খেলা খেলত সে । ছুচে সুতো পরানোর খেলা । সরু ছুচের ছোট্ট ফুটো দিয়ে সুতো গলানো খুব সহজ ছিল না । কে পারে এক চান্সে ? একশো ওয়াটের কাঁপা কাঁপা আলোয় ! রিল থেকে সুতো ছুচে পরানোর পর সেটাও দাঁত দিয়ে কাটা হত । সুতোর মুখ অসমান হয়ে যেত । সুতোর অত সরু শরীরেও তৈরি হত ফাটল । সুতো আর উপসুতোয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত রিলের মুখ । ছুচের ফুটোয় হয়তো উপসুতো ঢুকত, মূল সুতো নয় । সুতোর শরীর তখন আরও খানিক বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম । যে মুখ দিয়ে রিল থেকে ছিন্ন করা হত ছুচ সুতোর অংশ সেই মুখ দিয়েই রিলের সুতোকে সুস্থ করা হত । জিভ বুলিয়ে সুতো ও উপসুতোকে থুতোর আঠায় খানিক সময়ের জন্য এক করে দেওয়া । সেই ফাঁকে গলিয়ে দেওয়া ছুচে । সেলাই শেষ হতে হতে রাত । লোডশেডিং হলে খুব সাবধানে হেরিকেনের আলোয় খুঁজে গুছিয়ে নেওয়া সেলাইয়ের সরঞ্জাম ।
বড়ো সেলাইগুলো একটু একটু করে জমিয়ে রাখা হত সেলাই মেশিনের জন্য । সেই সেলাই মেশিন ছিল ওপরে , বাড়ি যাদের সেই জেঠিমার শোওয়ার ঘরে । দুপুর বেলা জেঠু যখন কলেজে , তার বাবা যখন অফিসে, মা আর মায়ের পেছন পেছন সেলাইয়ের নানা কাপড় নিয়ে সে জেঠিমার ঘরে হাজির হত । তাদের নিচের ঘরে যন্ত্র বলতে শুধু রেডিও, তাই সেলাই মেশিন ছিল তার কাছে অদ্ভুত এক যন্ত্র । বাবা সেটা চালাতে পারে না , ওপরের জেঠুও সেটা চালাতে পারে না , জেঠিমাও তত ভালো পারে না , পারে শুধু তার মা । এই যন্ত্র মাটিতে নামিয়ে তার সামনে বাবু হয়ে বসে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করা যায় আবার চাইলে চেয়ার বা টুলে বসে পা দিয়ে চালানো সম্ভব । মা চেয়ার বা টুলে বসেই সেলাই মেশিন চালায়, যেমন চালায় রঞ্জিত স্টোর্সের উলটো দিকের এ ওয়ান টেলার্সের দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা । পুজোর আগে তার ছোট্ট দোকানে কী কাস্টমার কী কাস্টমার ! একদিকে মায়ের পা চলে । অন্যদিকে মায়ের হাতের টানে সেলাইমেশিনের ছুচের তলা দিয়ে বয়ে যায় বাবার নতুন লুঙ্গি , কাজের মেয়ের সেমিজ, সদ্যকেনা সুটকেশের ঢাকার জন্য কাটা কাপড়, মায়ের নিজের জন্য করা মার্কিনের সায়া, সিন্থেটিক শাড়ির ফল্স । এই সব সেলাই একটানে হয়ে যায় । আর সে জানে প্রতিটা সেলাই খানিকটা করে টাকা বাঁচায় । সুটকেশের কেনা ঢাকার থেকে বানানো ঢাকার দাম কম, রেডিমেড সায়ার থেকে মার্কিনের সায়ার দাম কম । ওপরের জেঠিমার সেলাই মেশিন ব্যবহার করত বলে মা কাজের ফাঁকে ওদেরও একটা দুটো জিনিস সেলাই করে দিত । মেশিন ব্যবহার করে তেল দিয়ে সাফ সুতরো করে তবে মায়ের ছুটি । পা চলত , হাত চলত আর চলত মায়ের মুখ । ‘যেন দিদি বাবা তো ছোটোবেলায় মারা গিয়েছিল তাই বড়দি আর বড়ো জামাইবাবু আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল । জামাইবাবুকে সুনীলদা ডাকতাম । ওদের বাড়িতে একটা সেলাই মেশিন ছিল । অকশনে কেনা । তখন সুনীলদা অকশনে অনেক জিনিস কিনত । তা আমি সেটায় বুজু-কুটুর জন্য পাতলা ছিটের কাপড় কেটে জামা বানিয়ে দিতাম । গরমে খুব আরাম । কুটু যখন আরো ছোটো তখন শাড়ির পাড় সেলাই করে কাঁথা । যেন খুব সখ ছিল বিয়ের পর একটা সেলাই মেশিন কিনব । তা ওর বাবার তো বুঝতেই পারো । হয়ে ওঠে না। আমার মা খুব ভাল সেলাই করত । মনে আছে । ফলের ঝুড়ি ঢাকা দেওয়ার জন্য কী সুন্দর কারকাজ করা একটা ঢাকা বানিয়েছিল । বাবা তো ছবি আঁকত । মায়ের সেলাইয়ের জন্য নক্শা এঁকে দিত । আর এর বাবা । সারাদিন রেডিও কানে, গরমে ফুটবল । শীতে ক্রিকেট।’
হাত পা আর মুখের চলাচলে সেলাই সেলাই দুপুর শেষ হয়ে বিকেল আসত । সে মায়ের সেলাই করা কাপড় নিয়ে নিচে নামত । মা এবার ওগুলোকে ভাঁজ করবে, জায়গা মতো রাখবে । তবে জায়গা তো চিরকাল একরকম থাকে না । ছোটোবেলার প্যান্টের বোতাম একটু বড়ো হতেই বদলে গেল চেনে তখন আর অমন করে পোস্টাপিস খোলা বলে মায়ের কাছে যাওয়ার দরকার পড়ত না । জামার বুকের বোতাম কেন যেন ছিঁড়ে যেত না বড়োবেলায়, শুধু মাঝে মাঝে নিজেই ইচ্ছে করে খুলে রাখত সে বুকের বোতাম । বুকের বোতাম থেকে চলে গেল মা মা গন্ধ , মায়ের মুখের স্পর্শে ভিজে যাওয়ার অবকাশ হারাল সেই বোতামখানি । মাও ক্রমশ হারাল তার সেলাইয়ের উদ্যম, ছুচে সুতো পরাবার প্রখর দৃষ্টি । সেলাইয়ের কৌটো হারাল তার ঢাকা । মায়ের এই সেলাইয়ের সুতো ও বোতাম থাকত যাদের অঙ্গে তারাও তো ক্রমে সেলাইহারা হল । দাদা উড়ল বিদেশে । বাবা মিশল আকাশে । সে এখন মায়ের থেকে দূরে শান্তিনিকেতনে । সপ্তাহান্তে মায়ের কাছে যায় – ঢাকাহীন সেলাইয়ের কৌটোটাকে দেখতে পায় না আর ।
সাইকেল
এই লেখাগুলোর নাম মায়াময় । মায়া লেগে থাকে । গত আশির দশকের জীবন-যাপনে আমরা অনেক কিছু সঙ্গে নিয়ে চলতাম । ইয়ুজ করেই থ্রো করে দিতাম না । সেই লেগে থাকা জীবনের ছায়াছবি এই লেখাগুলোয়। এখন যে জীবন খোলাবাজার ও গোলকায়নের দাপটে রপ্ত করতে হচ্ছে তারই বিপরীতে এই অনতি অতীতের স্মৃতি । ‘মায়াময়’ এ তৃতীয় লেখা। সাইকেল চেপে শৈশব ঘুরে এলেন বিশ্বজিৎ রায় ।
সে জীবনে নিজেদের বাড়িতে প্রথম যে যানটি দেখেছিল তার নাম সাইকেল । ছোটো সাইকেল মানে ছোটোদের জন্য সাইকেল তখন পাওয়া যেত হয়তো কিন্তু সে পায়নি । পাওয়া অসম্ভব ছিল । কারণ তার বাবা রুমালে বেঁধে ট্রেজারি থেকে মাইনে আনত । সেই মাইনে এক দু তারিখে সন্ধেবেলা মা-বাবা ভাগাভাগি করতে বসত । এক একটা খামে এক একটা খরচের টাকা – বাজার, মাসকাবারি, পুজো, মঙ্গলাদি, ঘুঁটে কয়লা, দুধ, খবরের কাগজ, লৌকিকতা , মীরার হাতখরচ । এতে ছোটোদের সাইকেল কেনার জন্য কোনো টাকা বরাদ্দ ছিল না । সুতরাং তার জন্য আলাদা সাইকেল, ভাবতেই পারত না সে । তবে মীরার হাতখরচার টাকা জমতে জমতে একমাসে তার বাবাকে তার মা একটা সাইকেল কিনে দেয় । বি এস এ এস এল আর – ১৯৮২, চারশো টাকা । পুরুলিয়া শহরে এম এস ময়দানের ঘেরাও ডিঙিয়ে ডান হাতে একটা সাইকেলের দোকান ছিল । সেখান থেকে কিনে সাইকেল চালিয়ে বাবা বাড়ি ফেরে । সাইকেল তার জীবনে প্রথম ব্যক্তিগত যান ।
সাইকেল চালিয়ে বাবা বাজার যেত , দোকান, রেশন , তাকে স্কুলে পৌঁছে দিত সামনে বসিয়ে । সদাব্যস্ত এই সাইকেলটিতে ছোটো বলে তার প্রথম দিকে হাত দেওয়ার অধিকার ছিল না । বিশেষ করে সাইকেল গায়ের ওপর পড়ে গেলে সে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে এমন ভয় দেখানো হত তাকে । কিন্তু যা ভয়ের তা ক্রমশই কাছের হয়ে উঠল । স্পর্শই তার কারণ । বাবার সঙ্গে সে যখন স্কুলে যেত তখন অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেশ থাকত পেছনের কেরিয়ারে আটকানো । সে বসত সামনের রডে একদিকে পা ঝুলিয়ে । হাত দিয়ে ধরে থাকত হ্যান্ডেলের একাংশ । বাবার সঙ্গে মায়ের অগোচরে তার রফা হয়েছিল, সাইকেল চালাবে বাবা , বেল বাজাবে সে । সাইকেল বসে বেল বাজাতে বাজাতে তার ভয় ক্রমশই কেটে যায় । যার ওপর বসা যায়, যার বেল বাজানো যায় তাকে কি আর ভয় করা চলে ! সাইকেলের সঙ্গে স্পর্শের গভীরতা গভীরতর হয় এক রবিবারে । নতুন কেনা সাইকেল মাসে একবার দুবার মোছা দরকার । মায়ের কথামতো বাবা এক রবিবার বাদ দিয়ে সাইকেল মুছত । প্রথমে জল ভেজানো কাপড় দিয়ে সাফ-সুতরো করা হত সিট, হ্যান্ডেল, মাডগার্ড, স্পোক । তারপর শুকনো কাপড় দিয়ে দ্বিতীয় দফা মোছা । এই মোছামুছির কাজে সেও হাত লাগায় । প্রতিটি স্পোক মোছে ঝকঝকে করে । তাদের সাইকেলে দু একটা জিনিস ছিল না । যেমন আলো । এক আধজনের সাইকেলে সেই হেডলাইট সে দেখেছে । আলো থেকে তার সংযুক্ত হত ব্যাটারিতে । সেই ব্যাটারি লাগানো থাকত সাইকেলের পেছনের চাকায় । সাইকেলের পেছনের চাকায় আলো জ্বালানোর দরকার হলে কেসসহ ব্যাটারিটি ঠেলে লাগিয়ে দেওয়া হত । চাকার ঘোরা-ফেরায় ব্যাটারি লাগত তারে জ্বলে উঠত আলো । এই আলোজ্বলা সাইকেল কেনার পয়সা মায়ের নামে রাখা হাতখরচার খামে জমেনি বলে তাদের সাইকেলের পথে সন্ধেবেলায় আলো জ্বলে ওঠেনি । তবে তাদের টর্চ ছিল । বাবা সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছে , সে সামনে একদিকে পা ঝুলিয়ে বসে, হাতে টর্চ ।
বছর ঘুরতে না ঘুরতে সাইকেল মুছতে মুছতে সে একসময় সাইকেলকে আরও একটু নিজের মতো পাওয়ার সুযোগ পায় । তাদের ভাড়া বাড়ির সামনে ছিল একচিলতে ছোট্ট জমি । সেই জমির ওপর ছিল তিন তিনটে গাছ । একটা শিউলি, একটা সেগুন আর একটা কাগজফুলের । সেগুন গাছটা লাগানো নিয়ে ওপরের জেঠিমার সঙ্গে জেঠুর মতবিরোধ হয় । জেঠিমার মনে হয় সেগুন গাছ বাড়ির ভিত নষ্ট করে , জেঠু তা মনে করে না । সেই জমির ওপর তার সাইকেল যাত্রা শুরু পুজোর ছুটির সকালে । সাইকেল সে চালাতে পারে না , সাইকেলে চাপতেও পারে না কিন্তু সাইকেলকে সে হাঁটাতে পারে । সে হাঁটছে আর তার পাশে পাশে হাঁটছে বাবার জন্য কেনা বড়োদের সাইকেল – হাঁটছে না সে হাঁটাচ্ছে । প্রথমে টলমল করে পরে বেশ সাবলীল ভাবে সাইকেল হাঁটতে লাগল । সাইকেলের ওপর এরই মধ্যে টুপটাপ করে এসে পড়ল একটা দুটো ভেজা শিউলিফুল ।
সেই যে পুজোর সময় সাইকেলের সঙ্গে তার পথ চলার বোধন তারপর ক্রমশই কতরকম ভাবে যে সেই চলাচলের বিস্তার ! বাড়ির সামনের একচিলতে জমি থেকে সামনের কাঁচা রাস্তায় নামার অনুমতি মিলল শীতকালে । কিন্তু খবর্দার বড়ো রাস্তায় যাবি না বলে দিল মা । বেশ তাই সইল সে । তাদের পুরুলিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তায় থাকত বঙ্কা । বঙ্কাদের বাড়ি ছিল কাঁচা । বঙ্কার বাবার সাইকেল ছিল না , ছিল রিকশা । বঙ্কা সাইকেল হাঁটাত না, চালাত টায়ার । টায়ার সামনে চলছে আর বঙ্কা তার পেছনে ছুটতে ছুটতে একটা ছোটো লাঠি দিয়ে টায়ারকে ছোটাচ্ছে । বঙ্কার প্যান্টে বোতাম নেই , গায়ে গেঞ্জি । সে বঙ্কাকে অবাক হয়ে দেখে আর বড়ো রাস্তার আগে পর্যন্ত সাইকেল হাঁটায় ।
এরপর হঠাৎই একদিন সে সাইকেল সম্বন্ধে নানা কথা জেনে ফেলে । অনুরণ তার থেকে বয়সে বেশ খানিক বড়ো । সাইকেল চালিয়ে পড়তে যেত সে । সিটে বসে সাইকেল চালাত । সিটে বসে সাইকেল চালাতে গেলে নাকি প্যান্টের ভেতর আর একটা প্যান্ট পরতে হয় । সিটে বসতে পারে না যারা তাদের জন্য নাকি হাফ-প্যাডেল । হাফ-প্যাডেলের কথা ও সাইকেল সম্বন্ধে এতকিছু অনুরণ বলেছিল একদিন দুপুরে । শীতের দুপুর, স্কুল ছুটি । মা আর ওপরের জেঠিমা রোদে বসে গল্প করছিল । অনুরণ আর তাদের বাড়ির মাঝখানে সরু গলি । সেই গলিতে তাদের বাড়ির একটা জানলা ছিল । সেই জানলায় বসা যেত । অনুরণ গলিতে দাঁড়িয়ে, সে জানলায় বসে । অনুরণ বলেছিল হাফ-প্যাডেল শিখিয়ে দেবে । সাইকেলের রডের তলা দিয়ে একটা পা ওদিকে দিতে হবে, আর একটা পা থাকবে এদিকে । রডের ওপরে হ্যান্ডেলে থাকবে হাত । পা দিয়ে ঘট ঘট করে প্যাডেল ঠেলতে হবে । প্রথমে পুরো ঘুরবে না পা । প্যাডেলের চাপে সাইকেল এগোবে , পা নামাতে হবে । এভাবে একদিন ঠিক এগিয়ে যাবে সাইকেল । সেদিন বিকেলে সে হাফ-প্যাডেল চেষ্টা করে ও পড়ে যায় ।
যে কোনও পড়া যে শেষ পর্যন্ত ওঠার জন্যই তা সে টের পেল । পা কেটে গিয়েছিল, নুনছাল উঠে রক্ত পড়ে , সাইকেলের হ্যান্ডেল যায় বেঁকে । শান্তই কাকিমার মাঠে যখন এই সব হচ্ছে তখন বাবা রেডিওতে ভারত শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট ম্যাচের রিলে শুনছিল । সাইকেলের হ্যান্ডেল বেঁকে গেলে মা আস্ত রাখবে না আর সেটা যে তার পা কেটে যাওয়ার থেকেও খারাপ এটা বুঝতে পেরেছিল সে । তার ওপর থেকে সাইকেলটা সরিয়েছিল বঙ্কা । অনুরণ এসেছিল । তারা তিনজন সাইকেলটাকে দাঁড় করায় । অনুরণ সাইকেলের সামনের চাকাটাকে ওর দুপায়ের ফাঁকে চেপে ধরে । তারপর সেই অবস্থাতেই হ্যান্ডেলে চাপ দেয় । তার চোখের সামনে বাঁকা হ্যান্ডেল সোজা । বোঝার উপায় নেই বেঁকেছিল একটু আগে । সে বাড়ি ফেরে । ওঠা নুনছালের জন্য বকুনি খায় কিন্তু সাইকেলের জন্য বকুনি খেতে হয়নি । সাহস করে তারপর থেকেই সে হাফ-প্যাডেল, ঘট ঘট । পাড়ার কাঁচা রাস্তায় এগলি ওগলি । শীতকাল ঘন হয় । পুরুলিয়ার পাড়ার রাস্তায় কেমন ঝিম ধরা ধোঁয়া ধোঁয়া সন্ধে । বিকেলে সকালের খবরের কাগজ আসে । আর আসে আনন্দমেলা । আনন্দমেলায় ছবিতে গল্প থাকে । সে গল্প মা তাকে পড়ে শোনায় । সেই গল্পে সদাশিব বলে একটা ছেলের কথা থাকে । তার সাইকেল নেই, ঘোড়া আছে । নিজের নয় । কার একটা ঘোড়া সে যেন নিয়ে নিয়েছে । তার বন্ধু কুঙ্কু , আরও বন্ধু আছে সেবন্তী । তার মনে হয় সদাশিবের যেমন ঘোড়া তার তেমন সাইকেল । ঘোড়ায় অবশ্য হাফ প্যাডেল হয় না , তার সাইকেলে হয় । শীতের গলিতে রাস্তার আলো জ্বলে । বাড়ি ফেরে । মা ওয়ার্ড বুক খোলে । তার চোখে ইংরেজি নয় ভাসতে থাকে সাইকেল । কবে সে হাফ প্যাডেল থেকে ফুল প্যাডেল হবে । ট্রানস্লেশন ভুল হয়ে যায় । ঘুম পায় । বাবা রেডিওতে খবর শোনে । আনন্দমেলার সদাশিব নানা অভিযানে যায় । অনুরণ ফুল প্যাডেল, সাইকেলের সিটে বসে ঘোড়ার মতো এগোয় ।
পুরুলিয়ার পাড়ায় গোবিন্দলজের কাছে ছিল গোপাদির বাড়ি । বিকেল বেলায় গোপাদি খোলা চুলে রাস্তায় দাঁড়াত । গোপাদির হাতের নখ বড়ো ছিল । গোপাদি একদিন তার সাইকেল আটকে ছিল । সে গোপাদির হাতের ওপরে ব্রেক চেপে ধরে । গোপাদি সাইকেল ছেড়ে দেয় । সাইকেল আর ঘোড়া, ঘোড়া আর সাইকেল ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে ।
সে ঘুম তার ভেঙাছিল , হাফ প্যাডেল থেকে একসময় ফুল প্যাডেলও হয়েছিল কিন্তু আজকাল মনে হয় তার সাইকেলে, বড়োদের সাইকেলে ছোটোরা আর পা গলাবে না বলে হাফ প্যাডেল শব্দটা হারিয়ে যাবে । হাফ প্যাডেল মানে ছোটোও না বড়োও না । হাফ প্যাডেল মানে গোপাদির হাতে ব্রেক চিপে পাড়ার রাস্তায় শীত সন্ধ্যায় ঘট ঘট করে চলে যাওয়া ।
কুয়ো আর সেই লোকটা
এইলেখাগুলোর নাম মায়াময়।মায়া লেগে থাকে।গত আশির দশকের জীবন-যাপনে আমরা অনেক কিছু সঙ্গে নিয়ে চলতাম।ইয়ুজ করেই থ্রো করে দিতামনা।সেই লেগে থাকা জীবনের ছায়াছবি এই লেখাগুলোয়।এখন যে জীবন খোলাবাজার ও গোলকায়নের দাপটে রপ্ত করতে হচ্ছে তারই বিপরীতে এই অনতি অতীতের স্মৃতি।আশাকরি গাঁথতে পারব প্রতি মাস পয়লায়। মে মাসের প্রথমে ‘মায়াময়’র দ্বিতীয় লেখা। গরমে একটু আরামপাবে, কুয়ো আর সেই লোকটা’র কথা।লিখছেন বিশ্বজিৎরায়।
তাদের নিজের বাড়ি ছিল না , রানিং ওয়াটারের ব্যবস্থাও তখন জলকষ্টে ভোগা পুরুলিয়া শহরে ছিল না, কেবল একটা বহুরূপী কুয়োতলা খানিকটা ব্যবহারের অধিকার ছিল । সকাল বেলা বুড়ির মা আর মঙ্গলাদি সেখানে বাসন মাজত, কাপড় কাচত, চৌবাচ্চার জন্য জল তুলত । জল থই থই সেই চাতালে শীতের রোদ্দুর সাবানের ফেনায় ফেনায় আলতো পা বোলাত । রোদের পায়ে পায়ে সেই কাপড় ধোয়া ফেনা জল শান বাঁধানো চাতাল বেয়ে নালি পথে বাগানের মাটি ভেজাত । দোতলা বাড়ির পেছনের বাগানে কোণের দিকে যে পেঁপে গাছখানা নিজে নিজেই জন্মেছিল তার কাছে গিয়ে সেই সাবান জল একসময় থমকে যেত । জংলা ঘাস থেকে দুটো ফড়িং ঘাই মারত ।
তাদের ছিল একতলা, বাড়িওয়ালার ছিল দোতলা । বুড়ির মা কাজ করত ওপর তলায় , মঙ্গলাদি কাজ করত নিচের তলায় । ফলে বাসন মাজার, কাপড় কাচার আর জল তোলার প্রথম অধিকার ছিল বুড়ির মায়ের । মঙ্গলাদি আর বুড়ির মা সম্পর্কে ছিল দুই বেয়ান , বুড়ির সঙ্গে মঙ্গলাদির ছেলের বিয়ে হয়েছিল । সন্ধেবেলা পুরুলিয়া শহরে যখন খুব শীত পড়ত তখন খাটিয়ার তলায় রাখা ব্লাডার ভর্তি দিশি মদ তারা ভাগাভাগি করে খেত , একই শুয়োরের মাংস থেকে সুস্বাদু চাট বানাত । কিন্তু সকাল বেলা কাজে এলেই মঙ্গলাদি একতলা – বুড়ির মা দোতলা হয়ে যেত । শুধু একবার ঘোর শীতে খোয়ারি না কাটা এক সকালবেলায় মঙ্গলাদি যখন গরম চা খেয়ে আরও মাতাল হয়ে গেছিল তখন বুড়ির মা তার দোতলার অধিকার ভুলে লাল চোখ মঙ্গলাদিকে কুয়োতলায় নিয়ে গিয়ে বালতি বালতি জল ঢেলে ভিজিয়ে দিয়েছিল । কেমন যেন ঘোর লাগা চোখে ভিজে চুল ভিজে শাড়ি আলুথালু মঙ্গলাদি হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে থম মেরে গেল । তখন কুয়োতলায় আগে পরে, প্রথমে শেষে বাসন মাজার, সাবান কাচার, জল তোলার কোনও শব্দ ছিল না ।
ও বাড়ির পিছনে বাগান আর সামনে সদর দরজার একটু দূর দিয়ে চলেছে এক রাস্তা – সে বেশ চওড়া তবে পুরোপুরি পাকা নয় । সেই রাস্তা দিয়ে একটা লোক শীতকালে সাইকেল করে যেত । শরীরে তার খুব খাটো ধুতি আর গেঞ্জি , আর গেঞ্জির ওপর একটা কাঠের মস্ত ভি-মার্কা বোর্ড । সেই বোর্ডে খুব শীতও আটকে যেত । বোর্ডে লোকটার বুকের আর পিঠের দিকে একই রকম ভাবে লেখা থাকত দুটো শব্দ ‘কুয়ো ঝালাই’ । লোকটার মাথা জেগে থাকত সেই ভি-বোর্ডের ওপরে – সেখানে হাসি নেই, কান্না নেই , কথা নেই, বার্তা নেই শুধু সাইকেলে করে চলে যাওয়া আছে । এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় । সেই লোকটাকে থামানোর চেষ্টা করত ‘ওপর তলা’ , পারত না , ডাক পৌঁছত না রাস্তা দিয়ে যাওয়া লোকটার কানে । তখন নিচ তলা থেকে আমার মা গলা তুলে ডাকত ‘কুয়ো ঝালাই , ও কুয়োঝালাই ।’ সাইকেল থমকে যেত ।
তারপর কয়েক দিন বাদে যখন পুরুলিয়ার নীলকুঠি ডাঙার কাছাকাছি সাহেব বাঁধে সকাল বেলায় অনেক দূর থেকে এসে নামত ভিন দেশের অচেনা পাখির দল তখন একদিন সেই লোকটার সাইকেল এসে থামত দোতলা বাড়ির সামনে । আজ সে একা নয়, সঙ্গে তার আরও একজন । বুড়ির মা আর মঙ্গলাদি সেদিন চট করে কাজ শেষ করে ফেলত । আর সেই লোকটা একটা ছোটো লাল গামছা পরে , গায়ে তেল মেখে, কোমরে দড়ি বেঁধে উঠে দাঁড়াত কুয়োর পাড়ে । কুয়োর ভেতর — সে তো অনেক দূর । দুপাশে লাল খাবলানো ইঁট, আলো থেকে ক্রমে নিচে অন্ধকার – সেই ইঁটে সিঁড়ির মতো ধাপ খুঁজে নেয় ওস্তাদ লোকটার পা । আস্তে আস্তে নামে । ওস্তাদ যে সেই তো অজানা বিপদে ভরা নিচে নামতে পারে, যেতে পারে পৃথিবীর ভেতরের মাটির কাছাকাছি । সেখানে নাকি জল আছে, জলের তলায় কয়লা, কয়লার তলায় আগুন তারপর কী আছে কেউ জানে না – এ কথা বাবাকে অনেক অনেক জিগ্যেস করে শুধু জানতে পেরেছিলাম আমি । মা তখন কাছে ছিল না । সেখানে সেই তলায় কী যার–তার যাওয়া চলে ! লোকটার স্যাঙাত দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ওপরে । আর ওস্তাদ সেই পাতাল পথে নামতে নামতে কোথাও কোথাও ইঁটের ফাঁকে যেখানে গজিয়েছে আগাছা সেখানে থেমে গিয়ে দু হাতে সে-সব তুলে ফেলত । এভাবে একসময় সে পৌঁছে যেত কুয়োর শেষ তলায় ।
সেখানে শীতের কুয়ো ধরে রেখেছে জল । বর্ষায় নয় শীতে জল কম থাকে বলে সে সময় পুরুলিয়া ঝালিয়ে নেয় কুয়ো । না ঝালালে গরমে যে একটুও জল দেবে না এই শুকনো জেলা শহরের মাটি । ওস্তাদ সেই শীতের অল্প জলের কাছে গিয়ে তার কোমরের দড়িতে সংকেত দিত । সেই সংকেত দড়িপথে ঢেউয়ের মতো স্যাঙাতের হাত–দড়িতে দোলা দিয়ে যায় । আর সঙ্গে সঙ্গে কুয়োর কপিকল বেয়ে সে নিচে নামিয়ে দেয় বালতি । শুরু হয়ে যায় কুয়োমন্থন । নিচ থেকে বালতি ভরে দেয় ওস্তাদ , স্যাঙাত তুলে নেয় — ফেলে দেয় শানে । সেই কুয়ো সেঁচা জলে টানা ভিজতে থাকে বাড়ির পেছনের অগোছালো শীতের বাগান । বেলাবেলি সকাল থেকে ক্রমাগত দুপুর পর্যন্ত ভেজা । শেষ দুপুরের দিকে কুয়ো আর পরিষ্কার জল দেয় না – ঘোলা কাদামাখা জল তার শেষ সম্বল । তারপর একসময় কুয়ো যতটা জল ধরে রেখেছিল তা প্রায় ফুরিয়ে যায় । ওস্তাদ সেই প্রায় জলহীন কুয়োর শরীরের তলা তখন খুব যত্ন করে পরিষ্কার করে। সে সময় বাড়ির নিচের তলায় আমার মা ঘুমিয়ে পড়েছে । ওপরের তলায় কোনও আওয়াজ নেই । বুড়ির মা মঙ্গলাদি কাজ শেষ করে অনেক আগে চলে গেছে । বাবা অফিসে । শুধু আমার খড়ি ওঠা
হাফপ্যান্ট পরা পায়ে শীতের হাওয়া এসে লাগছে । পেঁপে গাছের হলুদ পাতা বাগানের ভিজে মাটিতে শব্দ না করে নামছে । কুয়োর শরীরের নিচতলা অবশ্য খুব বেশিক্ষণ জলহীন থাকে না । পুরনো জল সব ফেলে দিয়ে , ইঁট ঘেরা শরীরের আগাছা খুলে দিয়ে কুয়োকে সাফ সুতরো করে দেওয়ার পরই তির তির করে তার তলা ভাসিয়ে দেয় নতুন জলের ধারা । মাটির তলায় নাকি কোথাও কোথাও জলের গোপন মুখ থাকে – সেই গোপন মুখ আছে জেনেই এই খানে অনেক দিন আগে এ কুয়ো কেটেছিল এ বাড়ির লোক । তখন তারা ছিল নিচ তলার মানুষ । বাড়িওয়ালা হয়ে ওপর তলায় উঠে যায়নি । আমরা এখানে আসিনি ।
তির তির করে আসা এই নতুন জলের দিকে তাকিয়ে ওস্তাদ খুব খুশি হয় । যে বিড়িখানি নামার সময় তার কানে গোঁজা ছিল সেটা এবার আরাম করে কুয়োর ভেতরে বসেই ধরায় । শেষ দুপুর বিকেলের দিকে যায় । শীতের বেলা – আয়ু তার বেশি নয় । এবার আমার মা জেগে উঠবে , ওপর তলাও – আসবে তারা একসঙ্গে কুয়োতলায়, একজনের আগে আর একজন এমন ভাগাভাগির কথা মনে থাকবে না । কেমন ঝালাই হল কুয়ো তা যে দুই তলারই যাচাই করা চাই । বিড়ি শেষ করে তলার ওস্তাদ তখন ওপরে উঠে আসে । কোমরের দড়ি খোলে , তাকে একটা শুকনো গামছা দেয় স্যাঙাত । পড়ে আসা রোদে গামছা মাথায় উবু হয়ে বসে । তার দোসর কাগজের ঠোঙায় রাখা কলিচুন নিয়ে কুয়োর দিকে এগিয়ে যায় । তির তিরে জলে সেই চুন একটু একটু ছড়িয়ে দেয় । সারাদিন ধরে এই কুয়োকে সাফ করার টাকা বুঝে নিয়ে এবার চলে যাবে দুজন । হারিয়ে যাবে অন্ধকার নামার আগেই ।
তারপর সন্ধে হবে – নীলকুঠি ডাঙায় , সাহেব বাঁধে , আমাদের ভাড়া বাড়িতে ,দুলমি নডিহার এই বাড়ির কুয়োতলায় । বাবা আসবে । রেডিও চলবে । আর আগামী কয়েক দিন কুয়োর জলে পাওয়া যাবে অন্যরকম নতুন স্বাদ – চুনের । চুন নাকি কুয়োর পুরনো জলের সব দোষ ধুয়ে মুছে দেয় কিছু দিনের জন্য ।
————————
অলংকরণঃ নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
আঁচ
এই লেখাগুলোর নাম মায়াময় । মায়া লেগে থাকে । গত আশির দশকের জীবন-যাপনে আমরা অনেক কিছু সঙ্গে নিয়ে চলতাম । ইয়ুজ করেই থ্রো করে দিতাম না । সেই লেগে থাকা জীবনের ছায়াছবি এই লেখাগুলোয়। এখন যে জীবন খোলাবাজার ও গোলকায়নের দাপটে রপ্ত করতে হচ্ছে তারই বিপরীতে এই অনতি অতীতের স্মৃতি । আশাকরি গাঁথতে পারব প্রতি মাস পয়লায় । কদ্দিন তা অবশ্যি জানিনা। লিখছেন বিশ্বজিৎ রায়।
আগুন তো এখন সহজেই ধরানো যায় রান্নাঘরে । গ্যাস লাইটারের আগুনকে ওভেনের বুকে এখন ইচ্ছে মতো উসকে দেওয়া যায় , কমানো যায় দরকারে । আগুন ব্যবহারের এমন সহজ কল ও কব্জা সত্তর ও আশির দশকে বউটির ভাড়াবাড়ির রান্নাঘরে ছিল না । ক্রমে এল । নিভেও গেল অনেক কিছু।
রান্নাঘর । হলুদ দেওয়াল – এলামাটির । চল্লিশ পাওয়ারের টিমটিমে বাল্ব । এমন বাল্ব রান্নাঘর ছাড়া আর থাকত চৌবাচ্চাওয়ালা পিনপিনে মশা-ঘেরা বাথরুমে । তবে বাথরুমে থাকত না, রান্নাঘরে অতিরিক্ত থাকত বাল্বের গায়ে চিটচিটে ঝুল । বাল্বের ঠিক তলায় ছিল দেওয়ালে লাগোয়া পাতা উনুন। পাতা উনুনের একপাশে সিমেন্টের ধাপি । অন্যদিকে নালিপথ । কড়া ধোয়া জল যায়, যায় ভাতের ফ্যান সেই পথে । রোজ নয়, সপ্তাহে তিন-চারদিন ফ্যানের যাওয়া । অন্যদিনগুলোয় ফ্যান ধরে রাখা হয় কলাইয়ের পাত্রে । কাচা কাপড়ে দেওয়ার জন্য । তবে তার আগে ওই জমানো ফ্যান ছেঁকে শুদ্ধ করে নিতে হয় ।
সকালে তখনও সূর্য ভালো করে ওঠে নি । রাতের রান্নাঘরের সজাগ আরশোলারা তখনও বন্ধ করেনি তাদের ঘোরা-ফেরা, শরীরে-শরীর লাগানো । তখন উনুনে আঁচ পড়ে । সশব্দে প্রথমেই খুলে যায় রান্নাঘরের শেকল । দরজা খুলে বউটি ঘরে ঢুকতেই আরশোলারা চমকে যায় । এদিক ওদিক ছোটাছুটি, লুকনোর চেষ্টা । তাদের অগ্রাহ্য করে চল্লিশ ওয়াটের বাল্ব জ্বেলে দেয় মেয়েটি । তারপর সোজা উঠোনে । উঠোন বলতে পায়খানার বাঁধানো ট্যাঙ্কের ওপর । মজবুত, সুন্দর করে বাঁধানো । সেই উঠোন হিসেবে ব্যবহৃত জমির একদিকে গুছিয়ে রাখা কয়লা আর ঘুঁটের ঝুড়ি । কাপড় টাঙানোর নাইলনের দড়িতে একটা দুটো চড়াই । সকাল সূর্যের অপেক্ষায় । বউটি কয়লা আর ঘুঁটের ঝুড়িটি কোলে তুলে নেয় । তার শাড়ির আঁচল কোমরে গোঁজা । চড়াই দুটো উড়ে যায় । কাক ডাকে । একটা-দুটো মোরগ কোনোদিন । ঢলে পড়া মরা চাঁদ আকাশের গায় কোনো কোনো দিন । রান্নাঘরের আরশোলারা এই ফাঁকে খুঁজে নেয় নিরাপদ ফাঁক-ফোকর। জানে তারা পাতা উনুনের জেগে ওঠার সময় হল এবার।
উনুনের সামনে ঘুঁটে কয়লার ঝুড়ি । বড়ো মন দিয়ে এবার জ্বালানি সাজাতে হবে । এই সাজানোর যুক্তি, নিয়ম আছে । পুরুষেরা তা জানে না , চেনে না ঘুঁটে কয়লার নক্শা । যেমন তেমন করে সাজালে যে আগুন জ্বলবে না , আঁচ উসকে উঠবে না সে বোধ তাদের দিন-রাতে নেই । সাজাতে জানা চাই । লোহার শিকের ওপরে সবার আগে ঘুঁটের আস্তর পড়বে । গোটা প্রয়োজনে ভেঙে দু-আধখানা করে ঘুঁটে দেওয়া চাই । তারপর নানা মাপের কয়লা বুঝে-শুনে সাজানো । একের ফাঁকে অন্যের সমাবেশ । শিকের ওপর ঘুঁটে ও কয়লার নক্শা পাকা হলে নিচে বাঁধানো উনুনের মাটির গর্তে বাতিল ঠোঙা, কাগজ দিয়ে আগুন জ্বালতে হয় । সেই আগুনে ভাঙা হাত-পাখার হাওয়া দিতে দিতে একসময় তা লাফিয়ে উঠবে শিকের ওপর রাখা ঘুঁটে-কয়লার গায় । ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে সকাল হওয়ার আগের রান্নাঘর । মেয়েটির চোখ জ্বালা করবে । ঠোঁটের ওপর জমে উঠবে বিন্দু বিন্দু ঘাম । তারপর একসময় নীলচে-সাদা ধোঁয়া ফুরিয়ে যাবে । আগুন নিয়ে জেগে উঠবে উনুন । বাড়ির পুরুষের সকাল হবে । উনুনে রান্না বসবে ।
কখন কোন রান্না করা হবে উনুনে তারও হিসেব আছে একটা । আঁচ তো আর সারা সকাল একরকম ভাবে থমকে থাকে না । কখনও তেজ বেশি, কখনও তেজ কম । গনগনে, ধিকিধিকি । তেজ কমে গেলে আবার চারটি কয়লা ফেলে শিক দিয়ে খুঁচিয়ে দিলেই আগুন ঝলসে ওঠে বটে কিন্তু তার জন্য ঘুঁটে কয়লার মজুত চাই দস্তুর মতো । বাড়ির পুরুষের একার চাকরিতে , সে যতই সরকারি হোক, ইচ্ছে মতো কয়লা ফেলা যায় না উনুনে । সারাদিন উসকে রাখা যায় না আগুনের আঁচ । তাই কোন আঁচে কী রান্না হবে তার হিসেব করে নেওয়া চাই মনে মনে । বেশি আঁচে ডাল, তরকারি । বিশেষ করে ডাল । কড়ায় ডাল সেদ্ধ হতে সময় নেয় অনেক । মাছ মাঝারি আঁচে । ডাল তরকারির পর । মাছ ভাজতে যা সময় লাগে, কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চারা মাছের হলুদ ঝোল করতে কত আর আঁচ লাগবে । আঁচের ওঠা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিন এগোয় । ঠিকে ঝি আসে, যায় । ছেলে সকালের ইস্কুলে চলে গেল খাঁচা রিক্শায়, বাড়ির লোকটি অফিসের জন্য প্রস্তুতি নেয় । উনুনে সকালের আঁচ পড়ে আসতে না আসতে হাঁড়িতে ভাত চাপে । গব গব করে ভাত ফুটবে, নটা সাড়ে নটার মধ্যে ফ্যান গেলে ফেলতে হবে । ভাতের সঙ্গে একই হাঁড়িতে ফোটে আলু । একই সময়ে একই আঁচে সেদ্ধ হয় তারা । জ্বালানির খরচা বাঁচে ।
পুরুষটি কাজে গেলে রান্নাঘর পরিষ্কারের পালা । ঠিকে ঝি দুপুর-বিকেল ঘেঁষে আসবে, রান্নাঘর ধোবে জল দিয়ে ঘষে ঘষে । আর তার সেই ঘষার ফাঁকে ফাঁকে বউটি আলগোছে গল্প করে নেবে । গল্প করতে করতে বলবে, ‘মঙ্গলাদি নালির কাছটা একটু ভালো করে ঝাঁট দাও । ইঁটটা তুলে করে দিও । ফ্যানের সঙ্গে তো ভাত চলে যায় একটা দুটো । নালির গর্তের মুখে ইঁটের তলায় জমে । আবার ইঁটটা না দিলেও উপায় নেই । ইঁদুর, ছুঁচো ঢোকে । বাড়িওয়ালাকে বলেছি নালির মুখে লোহার ঝাঁঝরি বসিয়ে দিতে । কিছুতেই দিচ্ছে না। ’ মঙ্গলাদি ইঁট তুলে বসিয়ে দেয় । কিন্তু এসব তো দুপুরের কথা । খাওয়ার পরের গল্প । তার আগে ! রান্না শেষ হওয়ার পর যদি তখনও উনুনে আঁচ থাকে তাহলে কোনও কোনও দিন অবশেষ আঁচে চাটনি । ইচ্ছে না করলে জল ঢেলে আঁচ নিভিয়ে দাও সেদিনের মতো । তারপর নিভু উনুন ঠাণ্ডা হলে সেই ছাই থেকে যদি থাকে বেছে ফেল কয়লার অবশেষ । পুরো না জ্বলে যারা তখনও বেঁচে আছে তাদের জিইয়ে রাখা পরের দিনের জন্য । তবে এই সব কাজে ঢিলে ভাব । আলসেমি ভর করে থাকে । রান্নাঘরের একানে জানলার পেছনে পেঁপে গাছ । হলদেটে রোদ । পেঁপের শুকনো ডাল হাওয়ায় খসে । রান্নাঘর ছিটিয়ে রয়েছে, মেয়েটি ধাপিতে চুপ করে বসে । ছাই থেকে বেঁচে থাকা কয়লাদের বেছে তুলতে হবে, কিন্তু ইচ্ছে করছে না ।
টাকা যেখানে কম, ডাঁয়ে আনতে যেখানে বাঁয়ে কুলোয় না সেখানে অবশ্য ইচ্ছে করা আর না করা । যেমন করে হোক আগুন আর আঁচ জাগিয়ে রাখা । তার জন্য রোজ নিকিয়ে রাখা উনুন । রান্নার পর নিকিয়ে রাখলে পাতা উনুন ফাটে না , লোহার ঝিকগুলো দেখে নিতে হয় – খুলে আসছে কি না ! দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর মঙ্গলাদি চলে গেলে গুল দিতে বসা । কয়লা যেখানে জমিয়ে রাখা হয় সেই ঝুড়ির তলায় ধুলোর মতো জমে কয়লার গুঁড়ো । ওগুলো তো উনুনে দেওয়ার উপায় নেই । সেই গুঁড়ো কয়লা দিয়ে দুপুরবেলা এক-আধদিন গুল দেওয়ার পালা । গোল গোল করে পাকানো গুল উঠোনের একধারে শুকোয় সার সার । এরাও আগুনের পেটে যাবে আজ না হয় কাল ।
দিন নিভে আসে । রাতে এ বাড়ির রান্নাঘরে উনুন ধরে না । স্টোভ আছে । রেশনের কেরোসিন আছে । তবে রেশনে সব হপ্তায় ভালো কেরোসিন দেয় না । তলায় নোংরা । স্টোভে দেওয়ার আগে ছেঁকে নিতে হয় । নাহলে জনতা স্টোভ নষ্ট হয়ে যাবে । পাত্রের তলায় কালি পড়বে । স্টোভের আগুন নীল থেকে লাল হয়ে যাবে , লাফাবে – একটানা স্থির হয়ে জ্বলবে না । এই যে আগুন আর আঁচের ওঠাপড়া তা আশির দশকের শেষে ক্রমে মরে যায় । মেয়েটির রান্নাঘরে গ্যাস আসে । রিটায়ারমেন্টের পর নব্বইয়ের দশকে পুরুষটি নিজের বাড়ি করে । ক্রমে সেই রান্নাঘরে আলো, টিউব লাইট, প্রেসার কুকার, মাইক্রোওয়েভ । আলো আসছে – মেয়েটির বয়স হয়েছে, হচ্ছে । আঁচের ওঠা-পড়ার সেই যৌবনবেলা ক্রমশ অতীত । স্মৃতি । ছেলেরা দূরে । নিজের বাড়ির নতুন রান্নাঘরে আঁচ ও আগুনের খেলা ঠিক কীরকম এই বয়স কালে সে আর নতুন করে বুঝতে পারে না । সেই ঘেমে ওঠা শরীরের স্মৃতি আর অনুভূতি গত শতকের সত্তর-আশির দশকের রান্নাঘর থাকলে অনুভব করতে পারত, কিন্তু সেই সব রান্নাঘর তো সভ্যতার নিচে তলিয়ে গেছে । যে পুরুষটি জানত না কেমন করে কয়লা আর ঘুঁটে সাজালে আগুন উসকে ওঠে — তবু সেই আনাড়ি পুরুষটি, যে সঙ্গে ছিল — সেও আজ সেই টিমটিমে বাল্ব জলা রান্নাঘরের মতোই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে । তার রিটায়ারমেন্টের টাকার বাড়ি, বাড়ির রান্নাঘরে আজকাল একা একা রাঁধতে ইচ্ছেও করে না তার ।
আজই অর্ডার করো!

“কী লিখছি, কেন লিখছি, কার জন্য লিখছি এই তিনটি মন্ত্রই লেখা শুরুর মূল কথা”
কী লিখছি, কেন লিখছি, কার জন্য লিখছি এই তিনটি মন্ত্রই লেখা শুরুর মূল কথা- লেখা শেখার সহজ পাঠ কর্মশালায় শেখালেন রংগন চক্রবর্তী। খোলামেলা ধারণা নিয়ে চললে শেখার সু্যোগ বাড়ে। লেখার একটা কাঠামো তৈরি করে নিলে তরতর করে এগোতে পারবে, মাথায় যা আসছে লিখে ফেলা দরকার। হাতে কিছু থাকলে তবেই এডিট করবে। নিয়মিত লেখা ও লেখা নিয়ে ভাবনা চালিয়ে যেতে হবে, তবেই লেখা শেখা যাবে। এই আলোচনার PPT পেতে আমাদের ব্লগ ফলো কর: sahajpath.wordpress.com অথবা নিচের মেল আইডি তে মেল করতে পার।
সংবাদ লেখার গোড়ার কথা শেখালেন ভবেশ দাশ। সংবাদের ভাষা হবে সহজ, সংযত ও সংক্ষিপ্ত। লেখার প্রথমেই বুঝিয়ে দিতে হবে কি বিষয়ে লিখছ, প্রথম বাক্য টেনে নিয়ে যাবে দ্বিতীয় বক্যে, এবং দ্বিতীয় বাক্য নিয়ে যাবে তৃতীয় বাক্যে, এই আকর্ষণ ধরে রাখতে হবে শেষ পর্যন্ত।
কুমার রাণা আলোচনা করেন ফিল্ডের অভিজ্ঞতা কেমন ভাবে লেখায় পরিণত হতে পারে, চোখে যা দেখছি সেটা যথেষ্ট নয়, যা দেখছি তা তলিয়ে দেখতে হবে।
যারা এই কর্মশালার অংশগ্রহণ করতে পারনি, পরেরটায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছে জানিয়ে আমাদের মেল কর:sahajpath@outlook.com . কর্মশালার কিছু ছবি তোমাদের জন্য।
লেখা শেখার সহজ পাঠ
লেখা মানেই তো মহান লেখা নয়, অনেক সময়ই লেখা মানে যে কথাগুলো বলতে চাই, সেগুলোকে গুছিয়ে বলা, এবার সহজ পাঠে লেখা শেখার তার ভাবনাগুলো শেয়ার করল রংগন চক্রবর্তী।
লিখতে কি শেখা যায়? বললেই অনেকে বলবে মোটেই না। রবীন্দ্রনাথ হতে শেখা অসম্ভব। এক্কেবারে ঠিক কথা। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হতে শেখা যায় না। দরকারও নেই। কিন্তু লেখা মানেই তো মহান লেখা নয়, অনেক সময়ই লেখা মানে যে কথাগুলো বলতে চাই, সেগুলোকে গুছিয়ে বলা। সেটাও কিন্তু আমাদের চারপাশে খুব দেখা যায় না।
আমি যে সময় স্কুলে পড়েছিলাম, ষাটের দশকের শেষে আর সত্তর দশকের একেবারে গোড়ায় তখন আমাদের সাধারণ বাংলা মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সে রকম ভাবে লিখতে শেখানো হয়নি। ইংরেজিতে ‘এসে’ আর বাংলায় ‘রচনা’ অবশ্যই লিখেছি, কিন্তু লেখাটাকে ধরে কোন ও আলোচনা বা শেখানো স্কুলে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না। একটা নম্বর পেতাম, তাতেই ধরে নিতে হত ভালো, মন্দ না মাঝারি কী হয়েছে। আজকাল অনেক স্কুলে বোধ হয় শেখানো হয়, আমি ঠিক জানি না।
একটা সময় আমি ইংল্যান্ডে কিছু দিন পড়িয়েছিলাম, এই বছর দুয়েক। একটা স্কলারশিপের অংশ হিসেবে পড়ানোর কাজ ছিল। তখন কিছু ছেলেমেয়ের লেখা দেখে মনে হয়েছিল, এদের লিখতে শেখানো হয়েছে। কী করে একটা লেখা সাজাতে হয়, কী করে যুক্তিগুলোকে তুলে ধরতে হয়, কী বলতে চাইছি থেকে শুরু করে, এটা বলতে চাইছিলাম, তাই এটা বললাম ইত্যাদি একটা কাঠামোর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।
আমার একটা সুবিধে হয়েছিল যে পড়ার জগতের বাইরে একটা বাণিজ্যিক জগতে আমাকে লিখতে শিখতে হয়েছিল। যাদবপুর থেকে এম এ পাশ করে চাকরি খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞাপনে চাকরি পেয়েছিলাম। কপিরাইটিং-এর বা বিজ্ঞাপন লেখার কাজ। প্রথমে গ্রান্ট কিনিয়ন ইকহার্ট নামে এজেন্সিতে মধুচ্ছন্দা কার্লেকারের কাছে, পরে এইচ টি এতে নমিতা রায় ঘোষের কাছে কাজ করে কপি লিখতে শিখেছিলাম। সেই লেখার ট্রেনিং খুব কাজে এসেছিল।
তখন, এখনও নিশ্চয় আছে, বিজ্ঞাপন লিখতে শেখার নিয়মকানুনগুলো খুব মন দিয়ে শেখানো হত, যার থেকে যে কোনও লেখা লেখার একটা মূল কাঠামো শিখতে হত। আমার মনে আছে, এইচ টি এ বা হিন্দুস্তান থমসন অ্যাসোসিয়েটস, যেটা তখন দেশের সবচেয়ে বড় এজেন্সি ছিল, (এখনও বোধ হয় এক দুইয়েই আছে), সেখানে লেখার আগে মাথায় রাখতে হত চারটে প্রশ্ন: ১) আমি কার জন্যে লিখছি ২) তার মাথায় এখন আমার বিষয়টা সম্পর্কে কী ধারণা ৩) আমি কোথায় পৌছতে চাই এবং ৪) কী করে সেখানে পৌঁছব। ভেবে দেখ, এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে থাকলে কিন্তু অনেক লেখা বিশেষ করে যে লেখায় আমি কোনো বক্তব্য রাখতে চাই সেটা গুছিয়ে ফেলা যায়।
আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ, তাই নির্ভরযোগ্য নয়। তবে মনে হয় আমি ওই সময় চাকরি করতে করতেই, রাম রায়, যিনি পরে এইচ টি এ ছেড়ে নিজের এজেন্সি রেসপন্স খোলেন এবং এখনও রেসপন্স একটি সম্মানিত সংস্থা, তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন এবং সেই সময়টাতেই বিজ্ঞাপন তৈরির ক্ষেত্রে স্টিমুলাস আর রেসপন্স নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। তার মানে আমরা যেটা বলছি সেটা বেশি গুরত্বপূর্ণ না লোকে যেটা বলছে সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এর থেকেই প্রশ্ন ওঠে আমরা যা বলি লোকে কি তাই শোনে বা তাই মানে করে? বলা হয়েছিল না। উদাহরণ হিসেবে একটা কার্টুন দেখানো হত, একটি প্লেন এয়ারপকেটে পড়েছে, আর এয়ার হোস্টেস ছুটতে ছুটতে বলছে, প্যানিক কোরো না, প্যানিক কোরো না। প্রশ্ন হল, লোকে কী শুনছে? প্যানিক কোরো না, না কি প্যানিক করো, প্যানিক করো। এই সব নিয়ে নানান রকম মজার খেলা হত। একবার স্টিফেন কিং বলে বিজ্ঞাপনের এক গুরু এলেন। দিল্লির মৌর্য শেরাটন হোটেলে আমাদের দু দিনের ওয়ার্কশপ হল। বিজয়গড় থেকে মৌর্য শেরাটনের দুনিয়া, সে দারুণ লেগেছিল। ক্যাপিটালিজম বলে রাগও হয়েছিল, সেটা অন্য গল্প।
বিজ্ঞাপন জগতের বাইরে ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করতে গিয়েই পড়াশোনো করেছিলাম, অনেক, এই জগতেও লেখা শেখানো নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। আমি নিজেও শিখিয়েছি কিছু কিছু।
ভাবছিলাম, এই নিয়ে আবার ওয়ার্কশপ করাই যেতে পারে। আমার বন্ধু সাবিরও এই কাজ নিয়ে অনেক দিন লেগে আছে, আমরা দু জনে কিছু করতে পারি। সাবির আবার নতুন মিডিয়াকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে অনেক কিছু জানে, যে ব্যাপারে আমি এখনও খুব শিখতে পারিনি। তোমাদের কারও আগ্রহ থাকলে জানিও ই-মেল করে- sahajpath@outlook.com। একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।